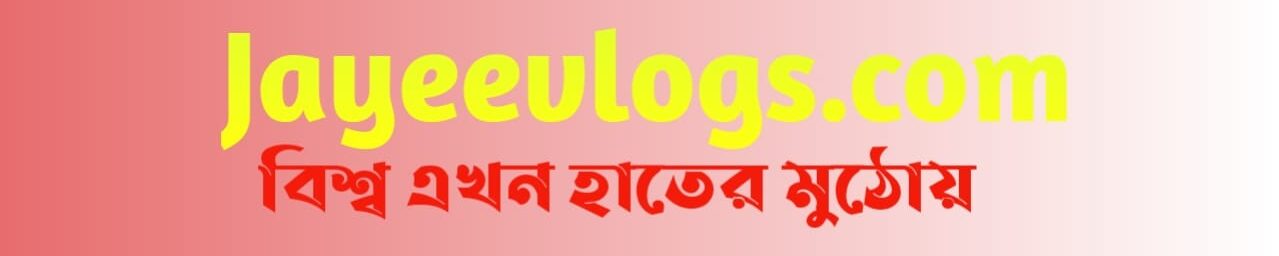২০২১ এ এসে আমরা বঙ্কিম-জীবনের ১৮৩ বছরে পদার্পণ করেছি। বঙ্কিম মারা গেছেনও বহুবছর হয়ে গেল। এত বছর ধরে বঙ্কিম নিয়ে আলােচনা হয়েছে বিস্তর; লেখালেখিরও অন্ত নেই। এত সেমিনার, এত আলােচনা-চক্র, এত প্রবন্ধ রচনার পরেও কিছু না বলা কথা থেকেই যায়। কখনাে কোনাে মুহূর্তে চোখে পড়ে বঙ্কিম জীবনের অনালােচিত অধ্যায়কে। তখন তাকে নিয়েই আলােচনা
আলােচনা বিচার বিচার ও বিশ্লেষণের সিদ্ধান্তে আসা। সম্প্রতি বঙ্কিম পরিবারের তিনজন নারীর চল্লিশটি চিঠি অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য ও পার্থপ্রতিম চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় বঙ্কিমভবন গবেষণাকেন্দ্র কঁঠালপাড়া থেকে প্রকাশিত হয়েছে। সম্পাদকদ্বয়ের দাবি হল বঙ্কিমভবন গবেষণাকেন্দ্র কাঠালপাড়ার দুর্লভ সংগ্রহ থেকে ‘একগুচ্ছ অতি পুরাতনজীর্ণ চিঠি তারা উদ্ধার করেছেন। আগ্রহ জাগে, ওই দুর্লভ সংগ্রহের বঙ্কিমজীবনের আরও কোনাে অজানা তথ্য লুকিয়ে আছে কিনা।
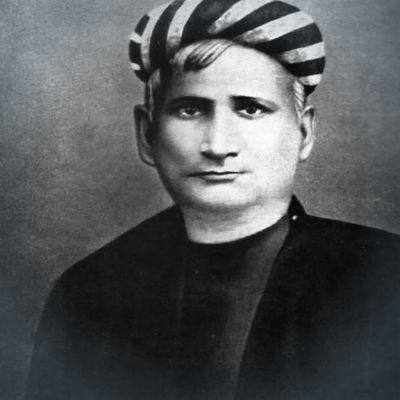
এই পত্রাবলীর মধ্যে সাহিত্যগুণ আছে কি না তা তর্কসাপেক্ষ। চিঠিগুলি উনিশ
শতকের বাংলাদেশের এক খ্যাতিমান পরিবারের মেয়েদের লেখা। এই চিঠিগুলি
সেই পরিবারের অন্দরমহলে প্রবেশের হাতছানি দেয়। চিঠি তাে শুধু যে লেখে
তারই পরিচয় দেয় না, যাকে লেখে তারও পরিচয় দেয়। আবার চিঠির অন্তরালে লুকিয়ে থাকে তৎকালীন সমাজের ছবিও। সংকলনের প্রথম চিঠি নন্দরাণী দেবীর।
বঙ্কিমচন্দ্ররা চার ভাই। শ্যামাচরণ,সঞ্জীবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র। তাঁদের যে নন্দরাণী নামে একজন বােন ছিল সে খবর আমরা ক-জন জানি? পিতা যাদবচন্দ্র ও মাতা দুর্গাদেবীর দ্বিতীয় সন্তান হলেন নন্দরাণী। জ্যেষ্ঠ শ্যামাচরণের পর তাঁর জন্ম হয়। নন্দরাণীর বিয়ে হয়েছিল শশিশেখর
মুখােপাধ্যায়ের সঙ্গে। যাদবচন্দ্র নিজের বাড়ির কাছে নন্দরাণীর একটি বাড়ি তৈরি করে দিয়েছিলেন। নন্দরাণী বেশির ভাগ সময়েই সেখানে থাকতেন। মাঝে মাঝে স্বামীর কর্মস্থলে যেতেন। নন্দরাণীর ছেলের নাম কৈলাস। মায়ের মৃত্যুর পর কৈলাস বাড়িটি বিক্রি করে দেন। নন্দরাণীর তারিখহীন একখানি চিঠি এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। চিঠিটি সঞ্জীবচন্দ্রের একমাত্র পুত্র জ্যোতিশচন্দ্রকে লেখা। জ্যোতিশচন্দ্রের স্ত্রী মােতিরাণীর চিঠিতে নন্দরাণীর নাম উল্লেখ আছে। মােতিরাণীর চিঠি থেকে জানা যায় নন্দরাণী, চট্টোপাধ্যায় পরিবারের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।
সেকালের প্রথা মতাে ওপরে শ্রীশ্রী দুর্গা’ লেখা এবং ‘পরম কল্যাণীয়’ বলে
জ্যোতিশচন্দ্রকে সম্বােধন করা হয়েছে এবং পত্রের শেষে ‘শ্রী নন্দরাণী দেবী’ লেখা রয়েছে। চিঠি থেকে জানা যায়, নন্দরাণী মাঘীপূজার আগে কাশীধামে গিয়েছিলেন এবং সেখানে চারমাস কাটিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছেন। চিঠিতে নন্দরাণী মায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। তথ্য-প্রমাণে দেখা যায় বঙ্কিমজননী দুর্গাদেবীর মৃত্যু হয়েছিল ১৮৭৩ সালে। সুতরাং এ চিঠিটি তার আগেই লেখা। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে যাদবচন্দ্র দানপত্র করে তার সম্পত্তি ছেলেদের মধ্যে ভাগ দেন। সম্পত্তি পৃথক হওয়ার
পরবর্তীকালে চিঠিটি রচিত হয়েছে বলে অনুমান করা যায়। চিঠিটির মধ্যে একটি
কঁঠাল গাছ ও সজনে গাছের উল্লেখ রয়েছে। এই দুটি গাছকে কেন্দ্র করে
অশান্তিরও ইঙ্গিত রয়েছে। চট্টোপাধ্যায় পরিবার পৃথক-অন্ন হলেও ছােটো খাটো
কারণে শান্তি ও সম্প্রীতি যে বিঘ্নিত হতাে এই চিঠিটি তার সাক্ষ্য দেয়।
দ্বিতীয় পত্র-লেখিকা বঙ্কিমচন্দ্রের পত্নী রাজলক্ষ্মী দেবী। সেকালে বাল্যবিবাহ
প্রচলিত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের এগারাে বছর বয়সে তার প্রথমবার বিয়ে হয়েছিল, পাত্রীর বয়স পাঁচ বছর, নাম সােহিনী। সােহিনী সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তবে তিনি খুব সুন্দরী ছিলেন। এগারাে বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হলে বঙ্কিম রাজলক্ষী দেবীকে বিয়ে করেন। রাজলক্ষ্মী দেবীর বাবার নাম সীতারাম বন্দ্যোপাধ্যায় ও মা মােহিনী দেবী। রাজলক্ষ্মী দেবী খুব সুন্দরী
ছিলেন না, তবে তার নানা গুণ ছিল। বারাে বছর বয়সে তার বিয়ে হয়েছিল এবং দীর্ঘ ৩৪ বছর তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে ঘর করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র একসময় বলেছিলেন চাকরি তার জীবনের অভিশাপ এবং তার জীবনের আশীর্বাদ হলাে বিয়ে করা। নবীনচন্দ্র সেনকে বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়েছিলেন ‘বিষবৃক্ষ’ উপন্যাসের সূর্যমুখীর চরিত্র রাজলক্ষ্মী দেবীর আদলে তৈরি। অন্যত্র তিনি আরও বলেছেন, তাঁর জীবনচরিত তাঁর স্ত্রীকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। দুঃখের বিষয়, কোনও বঙ্কিমজীবনচরিত থেকেই রাজলক্ষ্মী দেবী সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ৭১ বছর বয়সে রাজলক্ষ্মী দেবীর মৃত্যু হয়েছিল।
আলােচ্য পত্র সংকলনে রাজলক্ষ্মী দেবীর ৭ খানি পত্র সংকলিত হয়েছে।
সবকটি পত্ৰই জ্যোতিশচন্দ্রকে লেখা। রাজলক্ষ্মী দেবী আর বঙ্কিমচন্দ্রের কোনাে
পুত্রসন্তান ছিল না। তাদের তিন কন্যা—শরকুমারী, নীলাজকুমারী
উৎপলকুমারী। বঙ্কিম ও রাজলক্ষ্মী দেবী জ্যোতিশচন্দ্রকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন।
প্রথম চিঠিতে রাজলক্ষ্মী দেবী জ্যোতিশচন্দ্রকে ‘প্রাণাধিক পুত্র’ বলে
সম্বােধন করেছেন। চিঠিটি সম্ভবত ১৮৮০ সালের ১লা বৈশাখ লেখা। সম্ভবত বলছি
এই কারণে যে সম্পাদকদ্বয় চিঠির উপরে লেখা ‘১৮৮০ সালকে জিজ্ঞাসার চিহ্নে
চিহ্নিত করেছেন। ১৮৮০ সালে বঙ্কিম স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। তখন সঞ্জীবচন্দ্রের
সম্পাদনায় ‘বঙ্গদর্শন’ প্রকাশিত হচ্ছে। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী থেকে জানা যায় ১৮৭৯ সালে বঙ্কিম কঁঠালপাড়ার বাসা ত্যাগ করে হুগলির পাশে চুচুড়ায় একটি বাড়ি ভাড়া করে সপরিবারে বাস করছিলেন। পৈতৃক বিষয় সংক্রান্ত কারণে বঙ্কিম স্বগৃহ ত্যাগ করেন। কিন্তু অন্যত্র বাস করলেও যে কাঠালপাড়ার সঙ্গে যােগাযােগ বিচ্ছিন্ন হয়নি রাজলক্ষ্মী দেবীর চিঠি আর একবার সে কথাই জানালাে। চিঠি থেকে জানা যায় বঙ্কিমের অফিস বন্ধ থাকবে মনে করে রাজলক্ষ্মী দেবী কঁঠালপাড়া যাওয়া মনস্থ করেছিলেন, কিন্তু অফিস বন্ধ না থাকায় কন্যা শরৎকে একা রেখে তিনি যেতে পারলেন না। এই চিঠিটিতে বঙ্কিমের অপর দুই কন্যা নীলাজকুমারী বা উৎপলকুমারীর নাম উল্লেখ নেই। চিঠির নিচে ‘শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী’ লেখা হয়েছে।
দ্বিতীয় চিঠিটির তারিখ ১২৯৮ ১৮৮২, তলায় কোনাে স্বাক্ষর নেই।
চিঠিটিতে মামুলি কথাবার্তা। রাজলক্ষ্মী দেবীর সংসারে কাজের লােকের’ কষ্ট, তাই জ্যোতিশকে লােক পাঠাতে নির্দেশ দিয়েছেন। লােক পাঠানাের খরচ আপাতত জ্যোতিশচন্দ্র দিলেও তিনি যখন কাঁঠালপাড়া যাবেন, হাতে হাতে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
তৃতীয় চিঠিটি ১৮৯৩ সালে লেখা। নিতান্তই পারিবারিক চিঠি। সম্বােধনে এবার আর প্রাণাধিক পুত্র’ নেই, ‘পরম কল্যাণীয় শ্ৰীযুক্ত জ্যোতিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। দ্বিতীয় চিঠির পর প্রায় দশ বছর ব্যবধানে এই
চিঠি—সময় কি ‘প্রাণাধিক পুত্র’কে স্থানচ্যুত করেছে?
চতুর্থ চিঠিটিতে উপরে উল্লিখিত ঠিকানা ৫নং প্রতাপ চট্টোপাধ্যায়ের গলি।
বঙ্কিম-জীবনের শেষ অধ্যায় এই বাড়িতে কেটেছে। চিঠির তারিখ লেখা ১৮৯৭।
এখানেও সম্পাদকদ্বয় জিজ্ঞাসার চিহ্ন দিয়েছেন। ১৮৯৭ সাল হলে বঙ্কিমচন্দ্রের
প্রয়াণের পরে এ চিঠি রচিত। চিঠিটি বৈষয়িক। এখন আর প্রাণাধিক পুত্র’ নয়,
কল্যাণবরেষু। জ্যোতিশচন্দ্রের বেতনবৃদ্ধির জন্য সন্তোষ প্রকাশ করে লেখা হয়েছে, “তােমার মুড়ােগাছার ১২৫ টাকা লইয়া নলীন রাজনের দেনাশােধ দিয়াছে। নীলমণির কাছে আরও কিছু পাওয়া যাইবে। সে কলকাতায় আসিলে তাহার কাছে সে টাকা চাইব।” মুড়াগাছা হল বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগণার ডায়মন্ডহারবার মহকুমার অন্তর্গত একটি মৌজা। এখানে
বঙ্কিমচন্দ্রদের দেবােত্তর সম্পত্তি ছিল। ৫নং, ৬নং এবং ৭নং চিঠি অতি সংক্ষিপ্ত। ৫নং চিঠিতে বঙ্কিমচন্দ্রের
অসুস্থতার কথা উল্লেখ আছে। সে কারণেই জ্যোতিশচন্দ্রের চিঠি পেয়েও বঙ্কিম উত্তর লিখতে পারেন নি। রাজলক্ষ্মী দেবী জানাচ্ছেন বঙ্কিম এখন ভালােই আছেন এবং একটু সুস্থ হলেই তিনি উত্তর দেবেন। ৬নং চিঠিটি এই পত্রাবলীর মধ্যে একটু স্বতন্ত্র। সম্বােধন ‘চিরজিবেষু’ এবং শেষে তােমার ‘সেজখুড়িমা। এই চিঠিতে ‘ চিরজিবে’ বানান ভুলটি চোখে পড়ার মতাে। সেকালের দিনে অনেক সময়েই একজনের চিঠি আর একজন লিখে দিতাে। শােনা যায় বঙ্কিমের শেষজীবনে বঙ্কিমের সমস্ত চিঠির উত্তর রাজলক্ষ্মী দেবী লিখে দিতেন। বঙ্কিম শুধু স্বাক্ষর করতেন। তবে কি এই চিঠির
পত্রলেখিকা সেজখুড়িমা নিজের হাতে এই পত্রটি লেখেন নি? মূল পাণ্ডুলিপি না দেখার কারণে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। ৭নং চিঠিটিও অতি সংক্ষিপ্ত। শুধু জানা গেল জ্যোতিশচন্দ্রকে টাকা পাঠানাে হয়েছে। সেই টাকা জ্যোতিশচন্দ্র পেয়েছেন কিনা জানা না থাকায় আরও দশ টাকা পাঠানাে হয়েছে। শেষ হয়েছে তােমার শুভাকাঙিক্ষণী রাজলক্ষ্মী দেবী’ বলে। এই সংকলনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বাধিক সংকলিত ৩২টি চিঠি হচ্ছে জ্যোতিশচন্দ্রের পত্নী মােতিরাণী দেবীর।
মােতিরাণী সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। সঞ্জীবচন্দ্রের
একমাত্র পুত্র জ্যোতিশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। জ্যোতিশচন্দ্রের বয়স তখন ১৪ বছর এবং মােতিরাণীর বয়স আনুমানিক ৫/৬ বছর। মোতিরাণীর পিতৃগৃহ ছিল হাওড়ার
সালকিয়াতে। বঙ্কিমচন্দ্র এই বিয়েতে জাঁকজমক করতে বারণ করেছিলেন। তিনি
সঞ্জীবচন্দ্রকে চিঠিতে লিখেছিলেন, “আমার মতে জ্যোতিশের বিবাহ দুই বৎসর পরেও
ভাল, তথাপি ঋণ কর্তব্য নহে।” কিন্তু সঞ্জীবচন্দ্র কথা শােনেন নি। হাতির পিঠে
চড়ে জ্যোতিশচন্দ্র বিয়ে করতে যান। বিয়ের পরেও জ্যোতিশ চাকরি করতেন না।
সঞ্জীবচন্দ্রের মতােই তার চাকরি করার ইচ্ছা
ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রই জ্যোতিশচন্দ্রের একটি চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।
এই সংকলনে মােতিরাণীর ৩২টি চিঠি সংকলিত হয়েছে। এই চিঠিগুলিতে এক
প্রােষিতভর্তৃকা নারীর ব্যাকুল বিরহবেদনা প্রকাশিত হয়েছে। পাঁচটি সন্তান ও শ্বশুর-
শাশুড়িকে নিয়ে সংসার করার ছবি ফুটে উঠেছে। তৎকালীন যৌথ পরিবারের ছবি।
এই চিঠিগুলিতে ধরা পড়েছে। এই সব পরিবারের ভাব-ভালােবাসা, দায়িত্ববােধ,
স্বার্থপরতা, কলহ-কোন্দল চিঠিগুলিতে সবই আছে। সংকলিত এই চিঠিগুলির তাৎপর্য দূর-প্রসারিত, কারণ এই পত্রাবলী কোনাে সাধারণ পরিবারের নয়; উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী বঙ্কিমচন্দ্রের পরিবারের। মােতিরাণীর এই চিঠিগুলিতে ব্যক্তি মােতিরাণীর সুখ-দুঃখের সঙ্গে সঙ্গে। এই পরিবারের অন্দরের কাহিনিও দৃশ্যমান হয়েছে।
বঙ্কিমচন্দ্রের বাবা যাদবচন্দ্র ছেলেদের । পৃথক-অন্ন করে দিয়েছিলেন। কিন্তু পৃথক হলেও তাদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন কমে নি। চাকুরিজীবনে প্রতিষ্ঠিত বঙ্কিমচন্দ্র যে
সঞ্জীবচন্দ্রের পরিবারের কতখানি ব্যয়ভার বহন করতেন, চিঠিগুলি থেকে তার পরিচয় পাওয়া যায়। ৮নং পত্রে দেখি সঞ্জীবচন্দ্রের পেটের পীড়ার জন্য ‘সেজকাকা ঔষধ পাঠাইয়াছেন। ১২নং পত্রে রয়েছে, ‘ইতিমধ্যে একবার সেজকাকা আসিয়াছিলেন, আসিয়া তিনদিন থাকেন। ১ মন কলাই, ২০ সের ময়দা, ৮ সের ঘৃত, ৩ সের লবণ কিনিয়া দেন ও বাবাকে ৬২ টাকা নগত খরচের জন্য দিয়া যান।” ২৪ নং পত্রেও রয়েছে “সংসার খরচ সম্পর্কে সেজোকাকাকে সুরেশ পত্র লেখে তাহাতে
তিনি সমস্ত দ্রব্য আনাইয়া দিতে লিখিয়াছেন তাহাতে সুরেশ ১০ দিনকার সমস্ত দ্রব্য আনাইয়া দিয়াছে আর বাজার খরচের জন্য। সেজোকাকা ৪ টাকা পাঠাইয়াছেন।
বঙ্কিমচন্দ্র রাজলক্ষ্মী দেবীকে বিয়ে করার পরে চাকুরিস্থলের প্রায় সর্বত্রই তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছেন। জ্যোতিশচন্দ্র যে মােতিরাণীকে সঙ্গে নিয়ে যান নি, বঙ্কিমচন্দ্রের তাতে ঘােরতর আপত্তি ছিল।
২০নং পত্রে মােতিরাণী লিখছেন, “সেজোকাকা কল্য আসিয়াছেন, অদ্য
থাকিবেন… তুমি লইয়া যাইতে বিলম্ব করিতেছাে তজ্জন্য তাহার অতিশয় রাগ।
২৩নং পত্রেও এই বিষয়টি রয়েছে :
“সেজোকাকা পত্র লিখিয়াছেন যে তিনি
আর সংসার খরচ দিবেন না তাহার কারণ তুমি আমাদের লইয়া না যাওয়া। শুধু বঙ্কিমচন্দ্র নন, জ্যোতিশচন্দ্রের এই আচরণে সকলেই বিরক্ত : “ছােটকাকা যাইবার সময় বলিলেন, যে সে ছােকরা লইয়া যাইবে না, সে কাকাদের গলায় ফেলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছে।”
এই উদাহরণগুলি প্রমাণ করে যে কর্তব্যপরায়ণ বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবচন্দ্রের
পরিবারকে কতটা সাহায্য করতেন। তবু তাে অভাব ঘােচে না, ৩নং পত্রে
মােতিরাণী লিখছেন, “এখানে সংসার খরচের বড়ই কষ্ট হইয়াছে। কোনদিন
বাজার হয়, কোনদিন হয় না।” ৪নং পত্রে আছে মােতিরাণীর অসুস্থ পুত্র চিরঞ্জীতকে পুরনাে চালের ভাত খাওয়াতে হবে, চালের জন্য মােতিরাণী ছােটখুড়ি অর্থাৎ পূর্ণচন্দ্রের
স্ত্রীকে বললেন, কিন্তু চাল মিলল না। সেজঠাকুরপাে বলিলেন যে তবে তােমরা
আপনারা চাল আনাও অতএব আমি বড়ই আতান্তরে পড়িয়াছি কোথা হইতে চাল আনাইব অদ্য কয়দিন বড়বাবুর বাড়ি হইতে চাল আনাইয়াছি….
কিন্তু কল্য হইতে ত কোন উপায় নাই।” বঙ্কিমচন্দ্র সঞ্জীবচন্দ্রের
পরিবারকে সাহায্য করতেন কিন্তু জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্যামাচরণ একেবারেই সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলেন না। ২২নং চিঠিতে দেখি : “মা নিজে গিয়া জেঠামহাশয়ের নিকট তােমার অসুখের কথা সমস্ত বলিলেন, কিন্তু তিনি কোনাে মতেই স্বীকার পাইলেন না যে তাহার নিকট
টাকা আছে।” মােতিরাণীর বাস্তব বুদ্ধি ছিল প্রখর। বর্ণনাচ্ছলে তিনি চিঠির মধ্যে একটি বাস্তব সত্যকে তুলে ধরেছেন : “এবার ঝুলনের সময় সেজোখুড়ি এখানে ছিলেন। আমি তাহার কথা কোনােমতে কাটাইতে পারি নাই বরং মার কথার অমত হইতে পারি তথাপি সােজেখুড়ির কথার অমত হইতে পারিব না কেননা তাহা হইলে তিনি চটিবেন তাহাকে চটাইলে সেজোকাকাকে চটান হইবে। সেজোকাকা চটিলে আমাদের
আর দাঁড়াইবার স্থান নাই।”
মােতিরাণীর পরিবারে অভাব ও দারিদ্র নিত্যসঙ্গী। “এখানে সংসার খরচের বড়ই
কষ্ট হইয়াছে। কোনদিন বাজার হয় কোনদিন হয় না। জ্যোতিশচন্দ্রকে তিনি চিঠিতে
অনুযােগ করেছেন, “তুমি একটু মনে ভাবনা যে বৃহৎ ৰাড়িতে তিনটি স্ত্রিলােক … গুলি
ব্যয়রামি ছেলে লইয়া কি প্রকারে বাস করিতেছি।”
মােতিরাণীর চিঠিগুলির মধ্যে এক বিরহিনী নারীর বেদনা ও হাহাকার ফুটে
উঠেছে : “আমি তােমাকে ৮ মাস ছেড়ে আছি কিন্তু আর আমাকে এমন করিয়া
রাখিওনা যেমন করিয়া পার আমাকে লইয়া যাও”, অথবা “রাধাবল্লভ জানেন! আমি
কিরূপ দিবারাত্রি কাটাইতেছি, আমার একদিনে এক বৎসর হইয়াছে। যদ্যপি ঈশ্বর
পাখি হইবার কোন উপায় করিয়া দিতেন
আমি পাখি হইয়া তােমার নিকট যাইতাম।” মােতিরাণীর কাব্যিক মনটিও ধরা পড়ে
চিঠিতে : “তােমার মনে আছে জ্যোৎস্না রাত্রে দুইজনে ছাতে যাইতাম। জ্যোত্সার
আলােতে তােমার মুখ দেখিতাম। এখনও
সেই জ্যোৎস্না। তুমি কোথা… আমি কোথা।” “সুখ আমার কোথাও নাই
তােমাকে ছাড়িয়া গােলক বৈকুণ্ঠেও নাই।”
আগেকার দিনে এরকম প্রােষিতভর্তৃকা নারীর জীবন ছিল হাহাকারে ভরা। চট্টোপাধ্যায় পরিবারের মাতা, এরকম একটি পরিবারের বধূ হয়েও মােতিরাণী তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। বাংলাদেশে শাশুড়ি-বউ-এর খণ্ডযুদ্ধধ চিরকালীন ব্যাপার। চট্টোপাধ্যায় পরিবারও
তার ব্যতিক্রম নয়। বাঙালি ঘরের এই দ্বন্দ্ব চিত্রটি মােতিরাণীর চিঠিতে স্পষ্ট। স্বামী
জ্যোতিশচন্দ্রকে তিনি লিখছেন : “আমার জন্য তােমার মা কাশী যাইতেছেন… বােধ
হয় এ সম্বন্ধে তােমার বাবাও অদ্য পত্র লিখিবেন… তােমায় এই শেষ পত্র লেখা
বাবাকে পৰ্য্যন্ত এমন করিয়া তুলিয়াছেন যে
তিনি পর্যন্ত মার সঙ্গে যােগ দিয়াছেন… তােমার মা যদ্যপি যথার্থই কাশি যান তাহা হইলে আমি তােমার নিকট ও জগতের নিকট চিরকলঙ্কিনী হইব।” এই একই অভিযোেগ ২৬নং পত্রেও রয়েছে : “মা যে
সংসারের কি ভয়ানক অবস্থা করিয়াছেন তাহা বলিবার নহে।” ২৭নং পত্রে লিখছেন,
“আমি কোন কথা বাবাকে বলিতে পারিনা, তাহা হইলে মা ঠিক তাহার বিপরীত
করিবেন।”
মোতিরাণী লিখিত দুটি চিঠিতে বঙ্কিমচন্দ্রের ছােটো মেয়ে উৎপলকুমারীর মৃত্যু
সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়। উৎপলকুমারী দেখতে খুব মিষ্টি ছিলেন।
সবাই আদর করে ‘পলা’ বলে ডাকত। তার বিয়ে হয়েছিল মতীন্দ্রনাথ মুখােপাধ্যায়ের
সঙ্গে। মতীন্দ্র অত্যন্ত দুশ্চরিত্র ছিলেন। মােতিরাণীর ১১নং চিঠিতে পলার মৃত্যু
সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। সেখান থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হল : “গত কল্য মঙ্গলবার
বাঁশতলার বাটিতে পলা গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে। সেই নিমিত্ত বুধবার রাত ১১টায়
রাখাল বাবাকে বটকৃষ্টকে দিয়া লইতে পাঠাইয়াছিল। সে বলিয়া পাঠায় আমি
একলা সেজবাবুকে সামলাইতে পারিব না। পলা মতীন্দ্রের জন্য প্রাণত্যাগ করিয়াছে। সে পিতামাতাকে পত্র লিখিয়া মরে। ঐ পত্র পুলিশে লইয়া যায়। এক্ষণে ঐ পত্র
সেজকাকার নিকট পাঠাইয়াছে।”
এ প্রসঙ্গে ২৯নং পত্রে মােতিরাণী আবার লিখছেন, “সেজকাকা কলিকাতায় আসিয়াছিলেন পলার মৃত্যু কিরূপে হইয়াছে জানিতে … পলা গলায় দড়ি দিয়া মরে নাই। সে মরিবার পর ডাক্তার সাহেব আসিয়া
তাহাকে কাটিয়া দেখিয়াছিল সে বিষ খাইয়া মরিয়াছে।” মােতিরাণীর চিঠি থেকে আরও জানা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের পত্নী রাজলক্ষ্মী দেবীর বারাে হাজার টাকার গহনা পলার কাছে ছিল। দুশ্চরিত্র মতীন্দ্র সেই গহনা নিতে চাইলে পলা দিতে অস্বীকার করে। সে কারণেই পলাকে মরতে হল। মতীন্দ্রর বাড়ির কাছে যে বিনোেদ ডাক্তার আছে বঙ্কিমকন্যা উৎপলকুমারীর মৃত্যু সে
যুগে রীতিমত চাঞ্চল্যকর ঘটনা হয়ে উঠতে পারতাে। কিন্তু কোনাে এক অজ্ঞাত কারণে
বঙ্কিম মতীন্দ্রকে আইনের চক্ষে দোষী সাব্যস্ত
করেন নি। শােনা যায় মতীন্দ্রর পিতামহর অনুরােধেই তিনি এ কাজ করেছিলেন। কিন্তু
শুধুই কি তাই? পারিবারিক সম্মান রক্ষাও কি বঙ্কিমের মনে স্থান পায় নি? বঙ্কিম
জীবনীকার লিখছেন, “পরে ব্যথিত পিতার কণ্ঠে অনেকবার শােনা গেছে তার কন্যার
বিষপানে মৃত্যুর কথা। বলতেন, আমিই কুন্দনন্দিনীকে বিষ খাইয়ে মেরেছি, আর
আমার অদৃষ্টে আমার মেয়ে বিষ খেয়ে
মরেছে।”
এই পত্রাবলী থেকে যেমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় তেমনি
অনেক কৌতুকের ছবিও চোখে পরে। ১৭নং পত্র থেকে জানা যায় সঞ্জীবচন্দ্রের
পরিবারে বােজ ৬ সের দুধ বরাদ্দ কিন্তু তার
অধিকাংশই সঞ্জীবচন্দ্র খান। মােতিরাণীর
ভাষায়, “বাবা খান দেড়সের, মা খান আধসের বাকি দুধ ছেলেরা খায় আমি দুই
চারিদিন অন্তর ১ পােয়া করিয়া খাই।” মজা শুধু এখানেই নয়, আরও মজার কথা হল :
“বাবার পেটের অসুখ বেশ সারিয়াছিল আবার কল্য হইতে পুনরায় পীড়া দেখা
দিয়াছে তাহার কারণ অদ্য দিন আষ্টেক হইল
আবার দুধ খাইতেছেন… এই কয়দিন হইতেে একেবারে দুই সের করিয়া দুধ খাইতেছেন।
তাহাও ক্ষীর করিয়া না হইলে খান না।”
পুত্রবধূর বিরহযন্ত্রণা সঞ্জীবচন্দ্রের উক্তি আরও কৌতুককর :
আমাকে যথােচিত তিরস্কার করিয়াছেন, তিনি আমাকে বলিলেন যে সেজকাকার নাম করিয়া সে বই লিখিয়াছে। তাহার মাথা লিখিয়াছে এই কথায় আমি
অতিশয় আশ্চর্য হইয়াছি। তিনি এই কথা
আমাকে কেন বলিলেন। কৃষ্ণকান্তের উইল
পড়িয়াছিলাম তাহাতে ভ্রমরের যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল বাবা হয়তাে মনে
করিয়াছেন যে আমি তাহার নকল করিতেছি।”
সঞ্জীবচন্দ্রের পুত্রবধূর প্রতি স্নেহশীল হৃদয়েরও পরিচয় পাওয়া যায় ৩২নং পত্রে। বধূমাতা দুধ খায় না বলে তিনিও দুধ খেতে চান না। ৩২নং পত্রে রয়েছে, “আমি দুধ
খাই না বলিয়া তিনিও দুধ খান না।” ৩২নং পত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা
যাদবচন্দ্রের শ্রাদ্ধের বর্ণনা পাওয়া যায় ।
“ঠাকুরদাদার শ্রাদ্ধে নৈহাটি, ভাটপাড়া,কাটালপাড়া ব্রাহ্মণ খাইয়াছে সব সমস্ত
ব্রাহ্মণ হইয়াছিল লুচি, ছােলার ডাল, কপি বেগুণ খাদ্য তালিকায় ছিল।”
এই আলােচনার শেষে এসে পৌছে মনে হয় এই চিঠিগুলি শুধু নানা তথ্যের
আকরই নয়, চিঠিগুলি আমাদের নতুন করে ভাবায়ও। এ কোন মেয়েদের আমরা দেখি
যাদের বাক্য বিন্যাসে বিরতি চিহ্নের ধারণা নেই, যারা বানান ভুল সম্পর্কে অবহিত
নন। উনিশ শতকের মধ্যভাগে সাধারণ পরিবারের গৃহবধূদের ক্ষেত্রে এই অজ্ঞতা
অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এই চিঠিগুলি যারা লিখেছেন তারা তাে সাধারণ পরিবারের
গৃহবধূ নন। তারা এমন একটি পরিবারের যে পরিবারে শুধু বঙ্কিমচন্দ্রের মতাে।
বুদ্ধিজীবীরই অবস্থান নেই, যেখানে রয়েছেন একাধিক জ্ঞানী-গুণী মানুষ। যাদবচন্দ্র ডেপুটি রেজিস্ট্রার। শ্যামাচরণ, সঞ্জীবচন্দ্র,বঙ্কিমচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র সকলেই সরকারি চাকুরির
উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত। আবার বঙ্কিমচন্দ্র শুধু সাহিত্যক্ষেত্রে নন, উনিশ শতকের বাংলা
সমাজ ও সংস্কৃতিতে, চিন্তা ও চেতনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। বঙ্কিমচন্দ্র
নারী-পুরুষের সাম্যের কথা বলেছেন। সাম্য’ প্রবন্ধে তিনি একাধিক বার নারী-
পুরুষের সাম্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। “মনুষ্যে মনুষ্যে সমান অধিকার বিশিষ্ট।
স্ত্রীগণও মনুষ্যজাতি অতএব স্ত্রীগণও পুরুষের তুল্য অধিকারশালিনী। যে কাজে
পুরুষের অধিকার আছে স্ত্রীগণেরও সেইকাজে অধিকার থাকা সঙ্গত।” নারী পুরুষের
অধিকারের সাম্য নিয়ে সে যুগে বঙ্কিমের মতাে কে ভেবেছেন? শুধু অধিকারের
নয়, নারীশিক্ষার প্রয়ােজনীয়তাও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু তিনিই আবার
নিজগৃহে অন্তঃপুরচারিণী নারীদের সম্পর্কে এত নীরব কেন? একখানি বইও তিনি।
জননী, জায়া, ভগিনী অথবা দুহিতাকে উৎসর্গ করেন নি। যে বঙ্কিম মেয়েদের।
সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে নানা প্রশ্ন তুলেছেন, তার পরিবারের মেয়েরা কেন
অন্তরালে রয়ে গেলেন? প্রদীপের নিচে এত অন্ধকার কেন? বঙ্কিম পরিবারের মেয়েরা
অন্তঃপুর-জীবনের সুখ-দুঃখ, ভাব- ভালােবাসা, কলহ-কোন্দল নিয়ে শুধুই ব্যস্ত
কেন? অন্তঃপুরের বাইরের বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের কোনাে খবরই তাদের উতলা করতে পারেনি।
বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন’-এর সম্পাদক।তার কঁঠালপাড়ার বাড়ি থেকে প্রচার ও
ভ্রমর’ নামে আরও দুটি পত্রিকা প্রকাশিত হতাে। বঙ্কিম পরিবারের কোনাে মেয়ের কোনাে লেখাই এই সব পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। ভারতী’ পত্রিকার সম্পাদকদ্বয়ের সঙ্গে বঙ্কিমের হৃদ্য সম্পর্ক। চন্দ্রমুখী ও
কাদম্বিনীর উচ্চশিক্ষার সাফল্যে বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দিত এবং গর্বিত। কিন্তু নিজের
পরিবারের মেয়েদের তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দিয়েছিলেন বলে জানা যায় না।
মেয়েদের তিনি পারিবারিক প্রথামতাে বাল্যবিবাহ দিয়েছিলেন। বঙ্কিম পরিবারে সদর ও
অন্দরের বিভাজন স্পষ্ট। এই বিভাজনকে দূর করে জীবনের রঙ্গমঞ্চে পাদপ্রদীপের ।
আলােয় মেয়েরা বেরিয়ে আসতে পারেননি।বঙ্কিম জীবনীকার ও সমালোচক
শিশিরকুমার দাশ তাঁর গ্রন্থের শিরােনামে তাকে চিহ্নিত করেছেন শৃঙ্খলিত-শিল্পী
হিসেবে। তিনি দেখাতে চেয়েছেন জীবনসত্যসন্ধানী বঙ্কিমের শিল্পীসত্তা সমাজের বিশ্বাস-
অবিশ্বাস, ভালাে-মন্দ ঔচিত্য-অনৌচিত্য, বিধি-নিষেধের লক্ষ্মণরেখা অতিক্রম করতে
গিয়েও শেষপর্যন্ত বার বার পিছিয়ে এসেছে। ব্যক্তি-বঙ্কিমের ক্ষেত্রেও এরকম
হওয়া আদৌ অসম্ভব নয়। আসলে শিল্পীসত্তা
তাে আর ব্যক্তিসত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়।প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই শত আমি-র
আবরণ। পারিবারিক ঐতিহ্য সময় সময় মানুষের সামাজিক অবস্থানকে নিয়ন্ত্রণ করে।
এমনও হতে পারে ব্যক্তি বঙ্কিম তার সময়ের সামাজিক অনুশাসনের বাইরে যেতে
আদৌ রাজি ছিলেন না। ধর্মতত্ত্বের গুরুরূপীী বঙ্কিম তাে একদিনে গড়ে ওঠেননি। এই আর একবার সেই কথাই মনে করায়।
সহায়ক গ্রন্থ
১. বঙ্কিম পরিবারের মেয়েদের চিঠি,
সম্পাদনা
অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য,
পার্থপ্রতিম চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমভবন
গবেষণা কেন্দ্র, কাঁঠালপাড়া, নৈহাটি,
জানুয়ারি ২০১৩
২. বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয়
শ্ৰীযােগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত, সাহিত্য
সংসদ, চতুর্থ মুদ্রণ ১৩৭৬
৩. বঙ্কিমচন্দ্র জীবনী, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, ।
আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, জানুয়ারি।